রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাষা ও রাজনীতিবিদদের দায়বদ্ধতা

গণতন্ত্র একটি বিকাশমান ধারা। গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়েই তা বিকশিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরও আমাদের দেশে গণতন্ত্র কতটা বিকশিত হয়েছে সে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চর্চার ব্যাপারে কতটা আন্তরিক সেটাও বিবেচ্য বিষয়। রাজনৈতিক চর্চার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র বিকশিত হয়। আর এতে প্রধান ভূমিকা থাকে রাজনৈতিক দলগুলোরই। এ জন্য রাজনৈতিক চর্চায় গণতন্ত্রের উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে এবং তা শতভাগ। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতেই একটি আস্থার সম্পর্ক তৈরি হয়। পরস্পরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।
নেতা-নেত্রীদের সম্মিলিত আচরণই আসলে সেই সমাজ বা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে সহায়তা করে। কাজেই নেতা বা নেত্রীর একক আচরণও এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ নেতা-নেত্রীদের আচরণ দ্বারা অন্যরাও উৎসাহিত হন। সেটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন। এ জন্য তাদের আচরণের মধ্যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় থাকতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরমতসহিষ্ণুতা এবং পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাষাতেও রয়েছে শিষ্টাচারের অভাব। কে কার চেয়ে বড়, কিংবা কাকে কীভাবে ছোট করা যায় সব সময় এ ধরনের হীন এবং অসহিষ্ণু মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় রাজনীতিবিদদের কথাবার্তায়। কিন্তু গণতান্ত্রিক একটি সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও মানসিকতা কোনো অবস্থায়ই কাম্য নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই আসলে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।
আমাদের দেশে এ ধরনের কর্মকা-ের চর্চা যত বাড়বে গণতন্ত্রের ভিত্তি ততই মজবুত হবে। প্রসঙ্গত ভলতেয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তির কথা স্মরণ করতে হয়। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তোমার মতের সঙ্গে একমত নাও হতে পারি, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য জীবনও দিতে পারি।’ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই ধরনের মানসিকতা প্রদর্শন করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিক বৈরিতাপূর্ণ সমাজে বাকসংযম এবং তাতে শালীনতা রক্ষা একান্ত অপরিহার্য। দেশের গুরুত্ব¡পূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ কথাবার্তায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন এমনটিই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মাঝেমধ্যেই এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে এবং তা প্রায়ই ব্যক্তিগত কাদা ছোড়াছুড়ি পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রায়ই একে অপরের প্রতি উসকানিমূলক বক্তব্য রাখেন। কথার ফানুস উড়িয়েই চমক সৃষ্টি করতে চান। জনসভায়, কিংবা টিভি টক শোতে জনতার হাততালি কুড়াতে অনেকেই কথার লাগাম টানতে চান না। এতে কেউ কৌতুক বোধ করেন, কেউ বা সস্তা আমোদও পান। কিন্তু বক্তার ব্যক্তিত্ব যে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটি কি সংশ্লিষ্টরা বুঝতে অক্ষম?
বর্তমান রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অনেক নেতা এমন ভাষায় কথা বলছেন যাতে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বালাই নেই। রাজপথ, সংসদ, জনসভা, টেলিভিশন টক শো কোথাও তারা কম যান না। বাকপটুতা প্রদর্শন করতে গিয়ে এমন সব প্রসঙ্গের অবতাড়না করেন যা অবান্তর এবং ব্যক্তিগত রেষারেষি, চরিত্র হনন ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব অসার তর্জন-গর্জনে আসলে দেশ ও জাতির কোনো উপকার হয় না। বরং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, প্রতিযোগিতা থাকবে, এমনকি অনেক সময় তা কৌশলাশ্রয়ীও হবে। কিন্তু তার মধ্যেও একটি সুস্থতা, মানবিকতা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে।
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বক্তব্য হবে ধী-শক্তিসম্পন্ন। মানুষজন বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা থেকে শিখবে, জ্ঞানার্জন করবে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি এখনও জাতিকে নতুন দিশা দেয়। তাই রাজনীতিবিদদের বক্তব্যে, কথাবার্তায়, আচার-আচরণে এমন বিষয় থাকা উচিত যা অনুসরণযোগ্য, প্রেরণামূলক ও জনকল্যাণকর। মাঠে-ময়দানের বক্তৃতায় অনেক সময় কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্য উত্তেজনাকর বক্তব্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সংসদে গিয়েও যদি একইভাবে কাদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত হয় রাজনীতিবিদরা এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে?
বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তাতে জনমনে নানা শঙ্কার সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাজনীতিবিদদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার কথা বলা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহল থেকে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ এবং অসহনশীল মনোভাবই দেশের রাজনীতির প্রধান চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দায়িত্বশীল পদে থেকেও এমন সব আচরণ কথাবার্তা বলা হচ্ছে যা সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে। এতে গণতান্ত্রিক চর্চা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু মানুষজন দেখতে চায় জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো অভিন্ন সুরে কথা বলছে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। বিশেষ করে সভা-সমাবেশের নামে রাজপথ গরম না করে, জনভোগান্তি না বাড়িয়ে মাঠে-ময়দানে দায়-দায়িত্বহীন বক্তব্য না দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা হোক।
দেশে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে শান্তিকামী মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়ে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বিশ্লেষকরা রাজনৈতিক সংঘাতকেই এ দেশের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি বলে মনে করেন। তাদের মতে, রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিতিশীল পরিবেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির চেয়েও ভয়াবহ। রাজনৈতিক অবিশ্বাস ও বিভক্তি এ দেশে অনেক গভীরে। বাংলাদেশের রাজনীতি কোন পথে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে বেশকিছু প্রশ্ন সামনে চলে আসে। এর মধ্যে প্রধান বিষয়টি হচ্ছে রাজনীতি এখন কাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। রাজনীতিতে আদর্শের স্থান কতটুকু। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা ইত্যাদি।
এটা সবারই জানা যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর রাজনীতির বিপথগামিতার শুরু হয়। নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে দিয়ে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রকৃত রাজনীতিবিদদের কাছে টানতে না পেরে দলছুটদের নিয়ে দল গঠন করলেন ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য। হালুয়া-রুটির আশায় অনেকেই ভিড়লেন সে দলে। দলছুটদের পেয়ে তার মনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। কীভাবে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা যায় তার জন্য নানা ফন্দিফিকির করতে লাগলেন। রাজনীতিবিদরা যাতে তার জন্য হুমকি না হতে পারেন সে জন্য তিনি এমন সব বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করলেন যাতে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি করাটা সত্যি কঠিন হয়ে পড়ল। তিনি নিজেই ঘোষণা করলেন, রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি কঠিন করার কথা।
যে ছাত্ররা ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা জনপ্রিয় করলেন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করলেন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করলেন সেই ছাত্ররাজনীতির উর্বর ভূমিতে রোপণ করা হলো স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতালিপ্সার বিষবৃক্ষ। অস্ত্র, টাকা আর ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ছাত্রদের একটি অংশকে দলে টানতে সক্ষম হলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। আরেক সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এসে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন। বিষবৃক্ষে জল ঢাললেন। অনেক ছাত্রনেতা ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারা পেয়ে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হলেন। এর মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতিতে কলুষতার ষোলকলা পূর্ণ হলো। ক্ষমতায় থাকা এবং যাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকল ছাত্র নেতারা। অনেকেই এমপি-মন্ত্রী পর্যন্ত হলেন। অস্ত্র-টাকা হাতে পেয়ে অরাজকতায় লিপ্ত হলো ওই ছাত্ররা।
ছাত্ররাজনীতিতে থেকে আদর্শ নামক বস্তুটি হারিয়ে যেতে থাকল। সেই সঙ্গে জাতীয় রাজনীতি থেকেও। কেননা সামরিক শাসন আমলে একটি নব্য ধনিক শ্রেণির সৃষ্টি হওয়ায় তারা ক্ষমতার অংশীদার হতে চাইলেন। টাকা দিয়ে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার সংস্কৃতি চালু হলো এবং আরও বেশি টাকা দিয়ে মন্ত্রিত্বের আসন কেনারও ব্যবস্থা হলো। এভাবে রাজনীতি চলে গেল ব্যবসায়িক শ্রেণির হাতে। নির্বাচনী ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ত্যাগী আদর্শবাদী রাজনীতিবিদরা অনেকেই রাজনীতির মাঠ থেকে ছিটকে পড়লেন। অন্যদিকে সামরিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী রাজনীতি ফুলেফেঁপে উঠল। এমনকি তারা ক্ষমতার অংশীদার পর্যন্ত হলো। শুধু রাজনীতি নয় ধর্মকে পুঁজি করে তারা ব্যাংক-বীমাসহ অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও স্থাপন করলেন।
ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনীতিতে ‘মৌলবাদের অর্থনীতি’ এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিল। রাজনীতিতে জায়গা করে নিল সাম্প্রায়িকতা। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হওয়ায় একটি সুস্পষ্ট বিভাজন সৃষ্টি হলো। সামরিক শাসকদের সৃষ্টি করা দলগুলো এই বিভাজনকে আরও প্রকট করে তুলল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তিকে এভাবে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে রাখা হলো। সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন এমনকি বিচার বিভাগকেও ক্ষতবিক্ষত করা হলো দলীয়করণের মাধ্যমে। এভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা ব্যাহত হতে থাকল। এরপর নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পর গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা শুরু হলেও সে পথও কণ্টকাকীর্ণ হয়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির হাতে ক্ষমতা ফিরে না আসায়। এক সামরিক সরকার হটিয়ে সেনাছাউনিতে জন্ম নেওয়া দলটিকেই আবার ক্ষমতাসীন করা হলো। এভাবে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে কার্যত সামরিক শাসকের উত্তরসূরিরাই ক্ষমতায় থেকে গেল। ফলে গণতন্ত্র কাক্সিক্ষত মাত্রায় বিকশিত হতে পারেনি।
এখনও আমাদের রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে এই এক জটিল আবর্তেই। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করাটা গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। বিশেষ করে যারা যখন বিরোধী দলে থাকে তারা নির্বাচনকালীন সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা চান। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি তো আসলে রাজনীতিবিদদের পরস্পরকে অবিশ্বাসের ফল। তিনটি জাতীয় নির্বাচন ইতিমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়েছে। কিন্তু এর ফলাফলেও পরাজিত দল সন্তুষ্ট থাকেনি। কখনো সূক্ষ্ম কারচুপি, কখনো স্থ’ূল কারচুপি, কখনো বা ডিজিটাল কারচুপির অভিযোগ তোলা হয়েছে। আর সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়ানোর কথা, দেখা গেল সেই সর্ষেতেই ভূত। এখন আবার সেই ভূতকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে আনার কথা বলা হচ্ছে। বিরোধী দল সংসদে অনুপস্থিত থাকছে। এর পরিবর্তে তারা সহিংস আন্দোলন-সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে। দেশের ভবিষ্যতকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ এক অনিশ্চিত গন্তব্যে। কিন্তু অচলায়তন ভাঙবে কবে?
পঞ্চম সংশোধনী পাস হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলোপ হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন হয়েছে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে রাজি হয়নি। নির্বাচন বর্জন করে তারা নির্বাচন বানচালের জন্য সহিংস কর্মসূচি পালন করে। নির্বাচনকেন্দ্রিক জটিলতা, হেফাজতের উত্থান, গণজাগরণ মঞ্চ, যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সালটা ছিল চরম সহিংসতার বছর। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের পর রাজনৈতিক সহিংসতা চরম আকার ধারণ করে। ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের প্রথম বার্ষিকীতে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা হরতাল-অবরোধ, পেট্রল বোমায় পুড়ে মারা যায় ১৩০ জনের বেশি মানুষ।
এর মধ্যে নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে ২০১৬ সাল। ইতিমধ্যে চার জন যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা, কামারুজামান, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসির দ- কার্যকর হয়েছে। নিজামীর আপিলের চূড়ান্ত রায়ও ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে ফাঁসির দ- বহাল আছে। এর মধ্যে দিয়ে যুদ্ধাপরাধের বিচার একটি পরিণতির দিকে যাচ্ছে। রাজনৈতিক বৈরিতার অন্যতম কারণও হচ্ছে আমাদের রাজনীতিতে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে একটি শক্তির অবস্থান। যা হোক, কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে কিংবা ক্ষমতায় থাকা না থাকার ইস্যুগুলোই রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে। সমঝোতার পরিবর্তে বৈরিতাই স্থান করে নিচ্ছে রাজনীতিতে। এ অবস্থা দেশকে এক সংকটজনক অবস্থায় নিপতিত করছে। কিন্তু এ অবস্থা তো কারও কাম্য হতে পারে না। তাই জনকলাণ্যের রাজনীতিই সবার প্রত্যাশা। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবেই।
এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বিকল্প হচ্ছে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন। এখন দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সরকার, বিরোধী দলসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের পর নির্বাচন কমিশন যেন সরকারের প্রভাবমুক্ত থেকে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে সেটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প হচ্ছে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন। এখন নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য দৃশ্যমান কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য সবার আগে নির্বাচন কমিশনের ওপর নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, নির্ভরশীলতা কমিয়ে কমিশনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে, যাতে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা রাখতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে কোনো সরকারই তেমন ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল বিরোধী দলে থাকলেই এই দাবিটি তোলা হলেও সরকারে গিয়েই তাদের সে অবস্থার পরিবর্তন হয়।
এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সংঘর্ষ আর বিভক্তির রাজনীতিতে থেকে বাংলাদেশকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশ চললেও এখানে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র ‘পরমতসহিষ্ণুতা’র যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতপার্থক্য বিস্তর। এছাড়া সংসদ বর্জনের রীতি এখানে রীতিমতো কালচারে পরিণত হয়েছে। যে দলই বিরোধী দলে থাকুক না কেন তারা নানা ছলছুতায় সংসদ বর্জন করে চলে। রাজপথে নানা কর্মসূচি দিয়ে জনভোগান্তি চরমে তোলে। অথচ সংসদই হওয়ার কথা ছিল সব কর্মকা-ের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও এখনো তা হয়ে উঠেনি। আশার কথা হচ্ছে, নানা বৈরিতা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক নানাক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। শিক্ষার হার বেড়েছে। কমেছে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার মতো আর্থিক ভিতও মঝবুত হয়েছে বাংলাদেশের। তথ্য-প্রযুক্তিখাতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। কিন্তু সে অনুযায়ী রাজনীতির গুণগত মানের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। এখনো মান্ধাতা আমলের ধ্যান-ধারণা নিয়েই চলছে এখানকার রাজনীতি।
বলা হয়ে থাকে রাজনীতি হচ্ছে নীতির রাজা। কিন্তু সেই নীতি যদি জনকল্যাণের পরিবর্তে জনস্বার্থকে বিঘœ করে তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বর্তমান বাস্তবতায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে রাজনীতি বাধা হয়ে দাঁড়াবে একবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের হঠকারী এবং অদূরদর্শী রাজনীতির কোনো স্থান নেই। রাজনীতিকে জনকল্যাণের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে সংসদ কার্যকর করতে হবে। তারও আগে নিশ্চিত করতে হবে সংসদে যাওয়ার সঠিক পন্থা। অর্থাৎ নির্বাচনী ব্যবস্থাটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অবশ্যই কার্যকর এবং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচনকেন্দ্রিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই রাজনীতিতে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং পাস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জায়গায়ও একটি গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তখন হয়ত কর্তাবার্তায়ও আসবে পরিবর্তন। শুরু করেছিলাম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাষা নিয়ে। আবার সেখানেই ফিরে যাই।
আসলে বক্তার বক্তব্য কতটা লম্বা হলো সেটা বক্তব্যের গুরুত্ব বহন করে না। বক্তব্য কতটা সারবত্তা হলো সেটাই দেখার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘অনেক কথা যাও যে বলি কোনো কথা না বলি’, না বলেও তো অনেক কিছু বোঝানো যায়। সেই বাকপটুতা এবং শৈল্পিক বোধটুকু থাকা অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে রাজনীতিও একটা আর্ট বা শিল্প। সংশ্লি¬ষ্টদের এক্ষেত্রে সেই শিল্প মনস্কতার পরিচয় দিতে হবে। তবেই রাজনীতি একটি গুণগত পরিবর্তনে আনা সম্ভব হবে।
লেখক : সাংবাদিক, টিভি উপস্থাপক














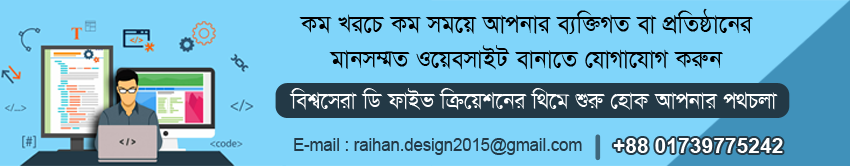




মন্তব্য চালু নেই