রক্তমাখা ঘরেই দু’দিন ছিল মধু দার পরিবার

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভেই পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সবার প্রিয় মধু দা। সে সময় হত্যা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-শিক্ষককে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, প্রিয় মানুষটি নিহত হওয়ার পরও দুদিন রক্তমাখা ঘরেই থাকতে হয়েছিল মধু দার পরিবারকে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিনের পরিচালক যিনি ‘মধু দা’ নামেই পরিচিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন তার ছেলে অরুন কুমার দে।
মধুর ক্যান্টিনের সূচনালগ্ন ১৯২১ সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মধুর ক্যান্টিনের যাত্রা ঠিক তখন থেকেই। তখন আদিত্য চন্দ্র দে (মধু দার পিতা) এ ক্যান্টিন চালু করেন। প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল কম। ছোট পরিসর গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আস্তে আস্তে ছাত্র-ছাত্রী বাড়তে থাকে। তখন ক্যাম্পাস এলাকায় কোনো ক্যান্টিন না থাকায় সবাই আসতেন মধুর ক্যান্টিনে। ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী বলে কোনো কথা নেই। সবাই এখানে আড্ডা দিতেন। ধীরে ধীরে মধুর ক্যান্টিন সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।
অরুন কুমার দে স্মৃতিচারণে বলেন, ‘স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক আগের কথা। সালটা ঠিক মনে নেই। মধুর ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠার ২০-২৫ বছর পর আমার ঠাকুরদা আদিত্য চন্দ্র দে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। তিনি সর্ম্পূণ শয্যাশায়ী হয়ে যান। এক কথায় কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। আমার বাবারা ছিলেন দুই ভাই। বাবার বড় ভাই অর্থাৎ আমার জ্যাঠা নারায়ন চন্দ্র দে। আর আমার বাবা হচ্ছেন আপনাদের সবার প্রিয় মধু দা, মধুসূদন দে।’
অরুন কুমার বলেন, ‘তখন বাবা ও জ্যাঠা দেশের বাড়িতে। স্কুলে পড়াশুনা করেন। ঢাকা থেকে খবর যায় আমার ঠাকুর দা (আদিত্য চন্দ্র দে) অসুস্থ্য। আমার বাবা ও চাচা দুজনেই চলে আসেন ঢাকায়। ঠাকুরদা ঠিক মত কথা বলতে পারছিলেন না। তখন আমার বাবা ও জেঠাকে ডেকে খুব ধীরে ধীরে বললেন, এ ক্যান্টিনের দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবা এবং ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সেবা করার দায়িত্ব নিতে হবে। তখন আমার জ্যাঠা সরাসরিই বলে দিলেন তিনি এ দায়িত্ব নিতে পারবেন না। আমার বাবা অর্থাৎ আপনাদের প্রিয় মধু দা তার বাবাকে আশ্বস্ত করেন যে, তিনি এ দায়িত্ব নেবেন। বাবার বয়স তখন ২০-২৫ বছর হবে।
তারপর আস্তে আস্তে যখন তিনি এ কাজ শুরু করলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মাচারীরা তখন আমতলায় (বর্তমান বটতলা) ছাত্র সমাবেশ ডেকে বাবাকে ‘সবার প্রিয় মধু দা’ খেতাবটা দেন।
ব্রিটিশ আমল গেল। এরপর পাকিস্তানি শাসন। তারপর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের যে প্রস্তুতি, সবকিছুই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনকে ঘিরে। বাবা তখন পুরোপুরি যুবক। এরপর ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট, ৬৬-এর ছয় দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যূত্থান, ৭০-এর সাধারন নির্বাচন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। তখন সব ছাত্র নেতারা ক্যান্টিনে আসতেন। আব্দুল মতিন, গাজিউল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ যারা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারা এবং পৃথক পৃথক দলের নেতারা কেন্টিনে আসতেন। ২৫ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবা ক্যান্টিনে ছিলেন। তখন পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল।
২৩, ২৪, ২৫ মার্চ পর্যন্ত পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটা থমথমে অবস্থা। ২৫ মার্চ বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় একটা ছাত্রসভা ছিল। ওই সভায় তোফায়েল আহমেদ, রাশেদ খান মেনন ও অন্যান্য নেতারা এলেন। সবাই ক্যান্টিনে চা পান করেন। এখান থেকে তারা শহীদ মিনারের দিকে যান। যাওয়ার সময় তারা বাবাকে একটা কথা বলে গিয়েছিলেন, মধু দা দেশের পরিস্থিতি কিন্তু খুব একটা ভাল না। একটু সাবধান হলে ভাল হয়। বাবাও তাদের আবার বললেন, আপনারাও একটু সাবধান হবেন।
হত্যাকাণ্ডের বিবরণ : ১৯৭১ সাল। ২৫ মার্চ মধ্য রাত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ক্যাম্পাস ঘিরে ফেলল। ২৫ মার্চ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সামনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসে অবস্থান নিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় হত্যার পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা টিএসসি থেকে ভাগ হয়ে গেল পুরো ক্যাম্পাসে। এক গ্রুপ গেল জগন্নাথ হলে, এক গ্রুপ গেল জহুরুল হক হলে, এক গ্রুপ এস এম হলে, আরেক গ্রুপ গেল রোকেয়া, শামসুন্নাহার হলের দিকে। আরো কিছু ভাগ হয়ে আবাসিক এলাকাগুলোতে গেল। রাত ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা নীরব নিস্তব্ধ। রাত সাড়ে ১২ টায় তারা শুরু করল নির্মম হত্যাকাণ্ড।
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে যেতে জগন্নাথ হলের বিপরীত পাশে হাতের বামে ৪ তলা ভবনটি। আমরা তখন দোতলায় থাকি। আমার বাবা-মা, বড় ভাই, বউদিসহ ১১ জন বাসায় ছিলাম। গুলির শব্দ শুনে আমাদের পরিবারের সবার ঘুম ভেঙে যায়। বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি লোকজন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে আর বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে। কর্মচারীদের ঘরগুলো সব দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলছে।
আর গুলির শব্দ তো চিন্তাই করা যায় না। মানুষের চিৎকার। জগন্নাথ হলের বর্তমান যে সীমানা দেয়াল সেটি তখন ছিল না। আমরা গুলির শব্দ শুনছিলাম।
ভোর হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ২৬ মার্চ ভোর ৬টা-৭টার দিকে আমাদের ভবনের সামনে মেইন রোডে আর্মির আট-দশটা গাড়ি। একটা গ্রুপ গেল গোবিন্দ চন্দ্র দেবের (জিসি দেব) বাংলোর দিকে। বাসাটি ছিল রাস্তার অপর পাশে। আরেকটা গ্রুপ আসল আমাদের বাসায়। আরেকটা গ্রুপ গেল শিব মন্দিরের দিকে। আর কিছু অংশ গাড়ি নিয়ে রাস্তায় অবস্থান করছিলো।
১০-১২ জনের একটা গ্রুপ আমাদের বাসায় চলে এলো। নিচে এসে জিজ্ঞেস করল বাবার কথা। মধু দা কোথায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্টাফ। ড্রাইভারের চাকরি করত। নাম ছিল তোতা মিয়া। হয়ত রাজাকার মাইন্ডের ছিল। সেই এসে বাসা দেখিয়ে দিয়েছে। বলেছে এ বাসায় থাকে। তখন তারা দোতলায় এসে বাসার দরজায় আঘাতের পর আঘাত শুরু করে। দরজা খোলার পর জানতে চায় বাবা কোথায়। বাবা কোথায় থাকে?
বাবা তখন ৪ তলায় ছিলেন। বলা হলো যে উপরে থাকে। তখন চলে গেল চার তলায়। ওদের ঊর্দু ভাষায় দরজা খুলো দরজা খুলো বলার শব্দ শোনা গেল। বাবা দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাবাকে ঘিরে ধরে। বাবাকে হাতকড়া পড়িয়ে পাশের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। চারিদিক থেকে বাবাকে ঘিরে দাঁড়ায়। বাবা হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরপর আমাদের ঘরে প্রবেশ করল মাত্র একজন সৈন্য। আর বাকি সবাই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। ওই একজন পুরো বাসায় সবকিছু তছনছ করে ফেলল। কাজি নজরুল ইসলামের ছবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি, বাবার সাথে তৎকালীন ভিসি আবু সাঈদ স্যারের ছবিসহ সবকিছু তছনছ করে ফেলল। র্যা গ ডে’তে ছাত্রছাত্রীদের সাথে বাবাও যে আনন্দের শামিল সেই ছবিগুলো সব নষ্ট করে দিল। ওই একজনই তাণ্ডব চালায় পুরো বাসায়। আর সবাই বাইরে গেটে দাঁড়িয়ে ছিল।
ছয় মাস আগে বিয়ে করেছে আমার বড় ভাই রনজিৎকুমার দে। বাবা খুব শখ করে উনাকে বিয়ে করিয়েছেন। বউদি রীনা রানী দে পাশের রুমে ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব সহজ সরল। গ্রামের মেয়েরা যেমন হয় আর কি। ঘরের ভেতরে যখন যায় বউদি তখন বসা। ওই অবস্থায় বউদিকে ধরতে যায় সেই সৈন্য। বউদি ছুটোছুটি শুরু করেন। বোন ছিল গেটের সামনে দাঁড়ানো। সে ভাইকে ডাক দেয়। দাদা, দাদা, বউদিকে মেরে ফেলতেছে। বড় ভাই এসে বলল হাত তোল, হাত তোল। কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাইয়ের বুকে গুলি। ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। এক পর্যায়ে বউদি বসে পড়লেন। ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন তিনি। ওই অবস্থায়ই বৌদিকেও গুলি। ভাই-বৌদি দুজনেই মারা গেলেন।
এরপর বাবাকে মারতে যায়। বাবাকে যখন মারতে যায় তখন আমার মা বাবাকে জড়িয়ে ধরেন। কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, আমারতো সবই শেষ করে দিলে। আমার স্বামীকে মেরো না। ওই অবস্থায় মায়ের সমস্ত শরীর গুলি করে ঝাঁজরা করে দিয়েছে। মা মারা গেলেন। মাকে মারার সময় দুইটা গুলি বাবার পায়ে লাগে। পরে বাবাকে ওইভাবে রেখে ওরা সবাই চলে গেল। এক ঘণ্টা পরে দুইজন বাঙালিকে নিয়ে আসল। ওরা লাশগুলোকে সরিয়ে নিল। পরে বাবাকে নিয়ে গেল। সামনে পেছনে পাকিস্তানি সৈন্যরা। আমি ওদের পায়ে ধরে বাবাকে নিয়ে যেতে বাধা দিই। সৈন্যদের একজন পায়ের বুট দিয়ে আমাকে জোরে লাথি মারে। পরে ওরা বাবাকে নিয়ে গেল জগন্নাথ হলের মাঠে। ওদিকে জগন্নাথ হল বাংলো থেকে নিয়ে আসে দর্শন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক গোবীন্দ চন্দ্র (জিসি) দেবকে। তিনিও গুলিবিদ্ধ ছিলেন। বাবা ও জিসি দেবসহ ছাত্র-শিক্ষকদের এক লাইনে দাঁড় করাল। সবাইকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করল।
এরপর ওখানেই মাটি খুঁড়ে বিরাট গর্ত করলো। আর ওখানেই মাটি চাপা দেয় সবাইকে। বিশ্ববিদ্যালয়েরই ৪-৫ জন কর্মচারী, যাদেরকে দিয়ে লাশ টানিয়েছিল তাদেরকে দিয়েই মাটি খোড়ানো হয়েছে।
পুরো বাসা রক্তে ভরা। এ অবস্থায় আমরা পুরো পরিবার দুদিন ছিলাম বাসায়। পরে আমরা চলে যাই দেশের বাড়ি বিক্রমপুরে। ওখানে আমার বড় বোন আর বড় দুলাভাই ছিল। সেখানে গিয়েও শান্তিতে থাকতে পারিনি। পরে আমার বাবার এক বন্ধু আমাদের সাভারে নিয়ে যায়। তিনি ১২ দিন রাখার পর আবার বিক্রমপুর পৌঁছে দিলে তারপরও থাকা সম্ভব হয়নি। রাজাকারদের সহযোগিতা নিয়ে ওখানেও খোঁজাখুঁজি। পরে রাতের অন্ধকারে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। সাতদিন-সাত রাত হেঁটে ভারতের ত্রিপুরায় উঠি। ওখানে ক্যাম্পে ছিলাম কিছু দিন। তারপর আত্মীয়দের বাসায় থাকলাম কিছুদিন। এভাবে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত ছিলাম। দেশ স্বাধীন যেদিন হয়েছে সেদিনই বাংলাদেশে চলে আসলাম। নতুন করে দায়িত্ব নিলাম মধুর ক্যান্টিনের।আবু বকর ইয়ামিন।














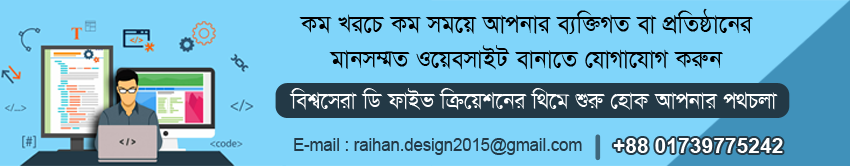



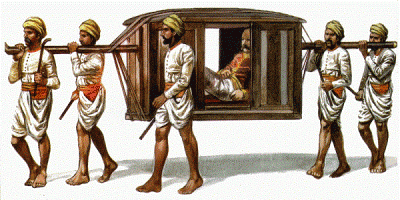














মন্তব্য চালু নেই