নভেরাকে আমরা জীবন্ত কবর দিয়েছি

কেউ জানলেন না কী হয়েছিল। নভেরা কেন চলে গেলেন। শোনা যায়, ষাটের দশকে দু-একবার তিনি দেশে ফিরেছিলেন। কেন এসেছিলেন, কোথায় ছিলেন তা আজও জানা যায়নি। ১৯৭০ সালে একটা প্রদর্শনী হয়েছিল তাঁর ব্যাংককে। বিজ্ঞজনরা তা দেখে বলেছিলেন, সে দেশে এমন এক ভাস্কর্য এর আগে আর হয়নি। তারপর নভেরা থিতু হলেন প্যারিসে। ১৯৬১ থেকে ২০১৫ অর্ধশতকেরও বেশি সময় প্রিয় স্বদেশ ছেড়ে বিভুঁইয়ে কাটালেন তিনি। অথচ তাঁর কীর্তিতে আকীর্ণ হয়ে আছে প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশ।
নভেরাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করেছি। এই প্রথম বাক্যের কাজটার কারণ উদ্ধার করতে হলে প্রায় ৩৮ বছর পেছনে ফিরে যেতে হয়। আমরা তখন নবীন যুবা। আমরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে। আর কী চাই! আমরা প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত এ দেশের সবচেয়ে নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তরুণ জীবনযাপনে আরো বেশি শিহরণ। আমরা অনেকেই ব্যাক-বেঞ্চার হলাম না। একেবারে দালানের পেছনেই চলে গেলাম।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গ্রন্থাগারের পেছনে তখন ঘোর-ঘোরাল আড্ডা। কেউ কথা বলত প্রচুর, আর সেই সঙ্গে টানত সিগারেট আর চা। কেউ শুধু কথা আর কথা। কেউ বা শুধু উন্নততর ভেষজ নেশা আর নীরবতা। কেউ বা আবার ট্যাবলেট খেয়ে যাপন করত নীরবতা আর নীরবতা। অদূরে পাণ্ডুলিপি ভর্তি গোল দালানের বাইরের দেয়ালে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ। সেখানে দেয়ালে দেহ ঠেসে দিয়ে তাদের প্রেম। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের নবীন মৌসুমি হাওয়ায় তাদের হৃদয়ে তখন আবেগের জোয়ার এসেছে। তারা দেহের উষ্ণতা বিনিময় করে নিজেদের বুঝছে তখন।
একটু দূরেই দুই দালানের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল পাথুরে মানুষ। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃক্ষের মতো শাখা-প্রশাখাময় দেয়ালের পলেস্তারা, ভাঙা ইট আর সুরকির দামে কারো বা দেহ খানিকটা ঢেকে আছে। বড় বড় মানকচুর গাছ ছিল। গাছের নিচে বসে ছিল এক নারী। শাড়িটায় খানিকটা মাথা ঢেকে দুই পা ভাঁজ করে যেভাবে প্রাচ্যের মানুষেরা বসে, সে রকম ভঙ্গিতে বসে ছিল সেই বাঙালি নারী। আরো কিছু পাথর ছিল শুধু জ্যামিতিক শরীর নিয়ে। তাদের ভাষা আমরা পড়তে পারিনি তখন। ভিজে স্যাঁতসেঁতে কচুতলায় দুর্গন্ধ! কুকুর, বিড়াল ও ছুঁচোর বিষ্ঠা আর প্রস্রাবের গন্ধ। আমাদের তখন কোনো বোধোদয় হয়নি। শিল্পবোধ-তা তো আরো সুদূরপরাহত। কেউ এসে আমাদের জানায়নি কিছু।
ধীরে ধীরে বড় হতে হতে জীবন বলে দিল এসব মানব-পুত্তলি এক নারীর শিলাকৃতি। নাম তাঁর নভেরা আহমেদ। সেই দূর পঞ্চাশের দশকে এই ভাস্কর শতাধিক ভাস্কর্য গড়ে এ দেশের আধুনিক শিল্পচর্চায় যোগ করেছিলেন বৈশ্বিক মাত্রা। আমরা যতটুকু আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি কিছু দিয়ে গেছেন নভেরা। ১৯৫৮ ও ১৯৬০ সালে দুটি ভাস্কর্য প্রদর্শনী করেছিলেন এই ভাস্কর-বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের ওই প্রাঙ্গণে। তখন পাশের দালানটি ছিল গণগ্রন্থাগার। কী করে এক নারী পঞ্চাশের দশকে এত ভাস্কর্য গড়তে পারেন। অনেক স্তুতি বাক্য বর্ষিত হলো। কেউ কেউ তাঁর শিল্পের মূল্যায়নেরও চেষ্টা করলেন তখন। কিন্তু তারপর নীরবতা।
কেউ জানলেন না কী হয়েছিল। নভেরা কেন চলে গেলেন। শোনা যায়, ষাটের দশকে দু-একবার তিনি দেশে ফিরেছিলেন। কেন এসেছিলেন, কোথায় ছিলেন তা আজও জানা যায়নি। ১৯৭০ সালে একটা প্রদর্শনী হয়েছিল তাঁর ব্যাংককে। বিজ্ঞজনরা তা দেখে বলেছিলেন, সে দেশে এমন এক ভাস্কর্য এর আগে আর হয়নি। তারপর নভেরা থিতু হলেন প্যারিসে। ১৯৬১ থেকে ২০১৫ অর্ধশতকেরও বেশি সময় প্রিয় স্বদেশ ছেড়ে বিভুঁইয়ে কাটালেন তিনি। অথচ তাঁর কীর্তিতে আকীর্ণ হয়ে আছে প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশ। তুষারাবৃত এক পাহাড় হিম অভিমান নিয়ে তিনি কেন মোহিত হয়ে রইলেন!
সত্তরের দশকের সেই তরুণ দিনের কথা মনে হয় আজও। অনুতাপে পুড়ে লেলিহান হয়ে যায় আমাদের জীবন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পেছনের প্রাঙ্গণে কান পাতলে এখনো কি শোনা যাবে না নভেরার কান্না অভিমানী মনের বেদনার গুঞ্জরণ। ভাস্কর্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিকে আমরা কী করে এতটা অবহেলার শিকার করলাম। এত শিক্ষক, এত গবেষক, এত সচেতন নাগরিক-কেউই কেন বুঝতে পারলেন না নভেরার এই শিল্পাকৃতির গুরুত্ব! শুরুতে বলেছিলাম, নভেরাকে আমরা আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করেছি। এখন আসল কথা বলি-নভেরাকে আমরা জীবন্ত কবর দিয়েছি। কবর দিয়েছি সেই প্রান্তরেই, যেখানে ১৯৬০ সালে তাঁর ৬০টি ভাস্কর্যের বিশাল প্রদর্শনী হয়েছিল। এই তো সেদিন চিরতরে নভেরা ছেড়ে গেলেন পৃথিবীলোক। আমরা কাঁদতে চেয়েছিলাম। বেহায়ার মতো। যাঁকে ভালোবাসিনি তাঁর মৃত্যুতে আমাদের কান্নার কী অধিকার আছে?
দুই
নভেরার জীবন কেউ লিখে রাখেননি। নভেরার শিল্প কেউ গভীর অভিনিবেশে পাঠও করেননি। ভাবা যেতে পারে, তাঁর রক্তবীজে শিল্পের যে চঞ্চল ইশারা ছিল, তা তিনি মায়ের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। নভেরার মা মাটি দিয়ে পুতুল বানাতেন। নিজের সৃজনে নিজেকে খুঁজতে গিয়ে নভেরা বারবার আঁতুড় দিনের সেই মাটির পুত্তলিকার কাছে ফিরে এসেছেন।
তবে তাঁর জন্ম সালটা ঠিক জানা গেল না। কেউ বলেন, ১৯৩০। কারো লেখায় তা ১৯৩৫। নভেরার জন্ম ১৯৩১ সালে হয়ে থাকে, তবেই তাঁর লন্ডনের শিক্ষাজীবন শুরুর জন্য বয়সটা সংগত মনে হয়। তাঁর বাবা খুলনায় কাজ করতেন। তখন সুন্দরবনের অদূরে কোনো মহকুমা শহরে হয়তো তাঁর জন্ম। তবে এ কথা সত্য, নভেরাদের আদিনিবাস চট্টগ্রাম। কলকাতার লরেটো স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেছেন। সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে তিনি লেখাপড়া করেছিলেন-এমন তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। বাবা চেয়েছিলেন মেয়ে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করুক। নভেরা তা চাইলেন না। তাঁর বড় বোন থাকতেন লন্ডনে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি সেখানে গিয়ে ক্যাম্বারওয়েল আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলেন। এ সময় শিল্পী হামিদুর রাহমানও থাকতেন লন্ডনে। দুজনের সঙ্গে একটা মানসিক সম্পর্ক তৈরি হলো। লন্ডনে থাকতেই নভেরা ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করলেন। ফ্লোরেন্সে গিয়ে অধ্যাপক ভেন্টুরির তত্ত্বাবধানে ভাস্কর্যশিল্পের তালিম নিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য ক্যাম্বারওয়েল স্কুলের পাঠ শেষ করেছেন তিনি।
দেশে ফিরে নভেরা আর হামিদ শহীদ মিনারের কাজ শুরু করেন। নভেরার ডিগ্রিটার নাম ‘ডিপ্লোমা ইন ডিজাইন ইন মডেলিং অ্যান্ড স্কাল্পচার’। সরকারের পূর্ত বিভাগের কাছ থেকে শহীদ মিনারের কাজটির ঠিকা এসেছিল হামিদুর রাহমানের নামে। ধারণা করি, হামিদদের পরিবারের প্রতিপত্তি ছিল বলে প্রশাসন থেকে কাজটি তাঁর নামে আদায় করে আনা সহজতর ছিল। শোনা যায়, হামিদ শহীদ মিনারের দেয়ালে ম্যুরাল করেন এবং মিনারের মূল স্থাপনার পরিকল্পনা নভেরার। যিনি ডিজাইনে ডিপ্লোমা ও ত্রিমাত্রিক শিল্প ভাস্কর্য বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন। তাঁর পক্ষেই সম্ভব মিনারের নকশা তৈরি করা। হামিদ ম্যুরাল করলেও কখনো ভাস্কর্য গড়েননি। সম্প্রতি বন্ধুবর আনা ইসলামের লেখায় বিষয়টির আলোকপাত দেখলাম। আনা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে নভেরা বলেছিলেন, ‘হামিদ তো ভাস্কর নয়, সে কী করে ডিজাইন করে। আমি মিনারের একটি ছোট্ট মডেল করে দিয়েছিলাম। হামিদের কাছেই আমার করা ড্রইংসহ সব কাগজপত্র ছিল।’ [শিল্প ও শিল্পী, জুলাই, ২০১৪]
শহীদ মিনারের থিম বিষয়ে আমাদের জানা বিষয়টা হলো দীর্ঘতম কাঠামোটি মা আর তার দুই পাশের কাঠামোগুলো সেই মায়ের সন্তান। দীর্ঘ উত্থিত গড়নটি আনত হয়ে আশ্রয় দিয়েছে সন্তানদের। গৌতম বুদ্ধের শান্তির মুদ্রাও নাকি এতে ইশারাময় আছে। নভেরা এ রকমই ভেবেছেন। আনা ইসলামের লেখায় এ বিষয়টিরও উল্লেখ আছে। ‘মা ও শিশু’ বিষয়টি নিয়ে সেই ১৯৫৭ সাল থেকেই যে নভেরা ভাস্কর্য রচনা করছিলেন তার অনেক প্রমাণই আছে আমাদের কাছে। আর তিনি বুদ্ধের কল্যাণমন্ত্রেও শোধিত করেছিলেন অন্তর। বুদ্ধুকেও একাধিকবার গড়েছেন নভেরা।
১৯৫৮ সালে ফার্মগেটের কাছে এক শিল্পপতির বাড়িতে একটি ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন নভেরা। ১৯৬০ সালে তাঁর বিশাল প্রাঙ্গণ ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর আগে এটিই তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ। ভাস্কর্যের বিষয়-একটি গরু আর দুটি মানুষ। মানুষ দুটি হয়তো বাবা ও ছেলে। তারা গরুকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, এমন ভাবা যেতে পারে। গরু ও মানুষের মিতালিতেই তো রচিত হয় কৃষি বাংলা। এ বিষয়টি নিয়ে চিত্র আঁকা হলেও তা পাথর কেটে ভাস্কর্যে রূপায়িত করার বিরল শিল্পদক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন নভেরা। কাজটিতে হেনরি মুর ও বারবারা হেপওয়ার্থের কাজের প্রভাব আছে। পঞ্চাশের দশকে পৃথিবীজুড়েই অনেক ভাস্করকে প্রভাবিত করেছেন মুর, হেপওয়ার্থ প্রমুখ ভাইটালিস্ট শিল্পভাবনার ভাস্কর। তবে সৃষ্টিশীল নভেরা বিষয় নির্বাচনে ও নির্মাণ কৌশলে স্বকীয়তাকেই পরিস্ফুট করেছেন।
নভেরার মাতৃকা ভাস্কর্য বিশেষভাবে দেখার বিষয়। তিনি অনেক নারীর অভিব্যক্তি গড়েছেন। তাঁর সবচেয়ে আদরের বিষয় মা। আঁচলে মাথা ঢাকা বাঙালি নারী আর শিশু-কাঁখে নারীর নির্মিতিতে বারবার পরখ করেছেন তিনি নিজের সৃজনশীলতা। বাংলার লোকশিল্পের পুতুল-মা তার সৃজন আবেগকে তরঙ্গায়িত করে রাখত। দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে পশ্চিমের আধুনিক ভাস্কর্যের রসায়নে তিন শিল্পের নবজন্ম দিয়েছেন। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ছেনির শিল্পিত প্রয়োগের দিকে তাকালে বোঝা যায় কেন তাঁকে ডাকতে হবে অপরাজিতা নামে।
নভেরার মৃত্যুর পর আনার ফোন পাই প্যারিস থেকে। নির্লজ্জের মতো কেঁদে ফেলি। টিভি চ্যানেলে ফোন দিয়ে জানাই নভেরার মৃত্যুর সংবাদ। একটু পরে মনে হলো, নভেরার মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করারই বা কী অধিকার আছে আমাদের। বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্যের বিস্ময়কর প্রতিভাদীপ্ত পথিকৃৎ মানুষটি মৃত্যুশয্যায় ঘুমের মধ্যে চলে গেছেন চিরঘুমের দেশে। তাঁর হৃদয় পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তটির কথা জানে শুধু সেই নিশীথিনী পেঁচা আর নীরব লাজুক কোনো সাপ। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দিন সখ্য হয়নি।














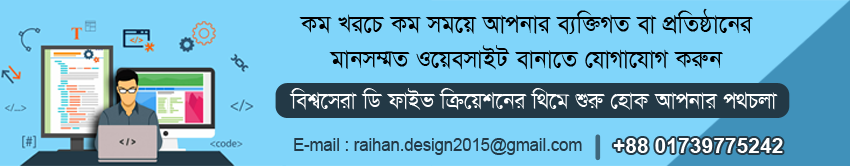



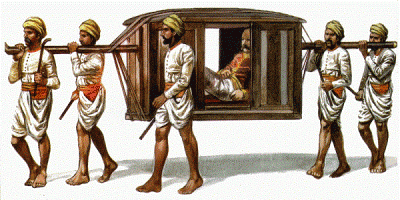














মন্তব্য চালু নেই